বাংলার শিল্পকলা ও সংস্কৃতি: Art and culture of Bengal.
ভূমিকা:
ভারতীয় ভূ-খণ্ডের পূর্বভাগে অবস্থিত বাংলা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক অংশে বিভক্ত ছিল যেমন গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট, সূক্ষ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। এই জনপদগুলিই পরবর্তীতে বাংলা নামে পরিচিতি লাভকরে। এই বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা ধরা হয় পূর্বভাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর ও উত্তর পূর্বে হিমালয় এবং পশ্চিমের মালভূমির কিয়দংশ নিয়ে। আর্য আগমনের আগে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলরা এখানকার অধিবাসী ছিল। কৃষি নির্ভর এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল। তৎকালীন অধিবাসীরা প্রাচীন দেব-দেবী ও লৌকিক আচার আচরণে নিমগ্ন ছিল এবং খাদ্যাভ্যাস ও ছিল নিজস্বধর্মী। তাম্রলিপ্ত চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি বন্দর শহরের মাধ্যমে মেসোপটেমিয়াসহ বহির্দেশে বাংলার বাণিজ্য চলত। মৌর্য বিজয়ের পর থেকে (300 খ্রীঃ পূঃ) এই অঞ্চলে প্রাচীন বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের প্রচার শুরু হয়। এই উত্তর ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও মাগধী প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, আচার, আচরণের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মৌর্য যুগের পর খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত সম্রাটদের আমলে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ তাদের অধীনে আসে। গুপ্ত শাসনের পর শশাঙ্ক বাংলায় রাজত্ব করেন তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তবে অখন্ড বাংলার চিত্র বা বাঙালি সত্ত্বার বিকাশ ঘটে পালযুগের সময় থেকে। পালযুগে মাগধী প্রাকৃত ও এই অঞ্চলে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার মিশ্রণে নতুন দেশীয় ভাষার উদ্ভব হল। বর্তমান বাংলা ভাষার এটাই হল আদিম রূপ যার নিদর্শন বৌদ্ধ পন্ডিতদের দ্বারা রচিত চর্যাপদ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনায় এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য-এই তিন জাতির মিলনে বাঙালী জাতীর সৃষ্টি হল। অখন্ড ভারতবর্ষের অঙ্গরূপে এই বাংলা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারক ও বাহক। বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এই অঞ্চলের মানুষ পৃথক পরিচয় সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন কাল থেকে বাঙালীর জীবন বিকাশ, জীবনচর্যা, ধ্যান-ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে স্বতন্ত্র সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি।
বাংলার স্থাপত্য:
গুপ্তযুগে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সমৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, পালযুগে তা আরও সমৃদ্ধ হয় ও স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে যা পূর্বরাগ বা Eastern School নামে পরিচিত। মৌর্য যুগের স্থাপত্য কলা থেকে বর্তমান যুগের স্থাপত্য কলার কালানুক্রমিক বর্ণনা করা হল-
প্রাচীন কালের স্থাপত্য:
মৌর্য যুগ থেকে ইসলাম আগমনের সময় পর্যন্ত শিল্প সংস্কৃতির একটি ধারা বজায় ছিল। তৎকালীন শিল্প রীতিকে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় যে সকল মন্দির ভাস্কর্য তৈরি হয়েছিল তা বেশীরভাগই ধ্বংস হয়েছে। বিভিন্ন বৈদেশিক বিবরণ শিলালিপি, তাম্রপট ও কিছু ধ্বংসাবশেষ থেকে তৎকালীন সময়ের স্তূপ, বিহার ও মন্দির এর স্থাপত্য বিবরণ পাওয়া যায়।
- স্তূপ: প্রাচীনকাল থেকে সমাধিস্থলে মাটিরস্তূপ তৈরির প্রচলন ছিল। বাংলার বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা ব্যাপকভাবে স্তূপ ব্যবহার করত। বৌদ্ধধর্মে সমাধিস্থলের পাশাপাশি গৌতমবুদ্ধের নির্দেশনা ও স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনায় এই স্তূপ তৈরি করা হত। নীচু গোলাকার বেদির উপর অবস্থান করত অর্ধচন্দ্রাকৃতি গম্বুজ। গম্বুজের ওপর হার্মিকার অবস্থান ও তার উপরে ছত্র বাছাতা এর অবস্থান ছিল। বাংলার বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত স্তূপগুলি হল-বর্ধমানের পানাগরের ভরতপুরের স্তূপ, ঢাকা জেলার আরাফপুরের ব্রোঞ্জের নিবেদন মূলক স্তূপ, রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্তূপ, বাঁকুড়া জেলার বাহলাড়া বৃহৎ স্তূপের ভিত্তিভূমি।
- বিহার: বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুকেরা বসবাস, শিক্ষাগ্রহন ও ধর্মপ্রচলনের জন্য এই বিহারগুলি ব্যবহার করত। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য বিদ্যার পরিচয় এই বিহার ও মঠগুলির মাধ্যমে পাওয়া যায়। ইঁটের সাহায্যে দুইতলা থেকে শুরুকরে নয়তলা পর্যন্ত বিহার নির্মিত হয়। এই বিহারগুলির কিছু ধ্বংসাবশেষ হল-
- মুর্শিদাবাদ জেলার কর্নসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহার।
- রাজশাহীর পাহাড়পুরের পালরাজা ধর্মপালের সোমপুর মহাবিহার।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের মোগলমারি বৌদ্ধ বিহার।
- মন্দির: মন্দির তৈরির বৈচিত্র্যময় রীতি এই বাংলায় প্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৈদেশিক আক্রমণ এবং সংরক্ষণের অভাবে প্রাচীন কালের স্থাপত্যের কিছু মন্দির অবশিষ্ট রয়েছে। প্রাচীন এই মন্দির গুলির মধ্যে প্রধান দুইটি গঠন রীতি নিম্নে বর্ণনা করা হল-
- রেখ বা শিখর দেউল: মূলভারতীয় মন্দির শৈলির একটি আঞ্চলিক রুপ হল এই শিখর মন্দির বা দেউল। মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা কুষাকৃত্তি হয়। স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী শিখর দেউলগুলি বাড়, শিখড়গন্ডি ও মস্তক দ্বারা গঠিত। মন্দিরের ভূমি থেকে খাঁড়া ভাবে যে অংশটি উঠেছে তাকে বলা হয় ‘বাড়’। ‘বাড়’ এর উপরি অংশে শিখড়গন্ডি অবস্থিত যা বক্রাকারে উপরে সমতলভূমিতে মিলিত হয়। এর উপরিভাগে অবস্থান করে মস্তক। মস্তক অংশে থাকে আমলকীর মতো ‘অলা’ ও তার উপরে থাকে কলস। উদাহরণ: বাংলার প্রাচীন মন্দির হল বর্ধমানের বরাকরের প্রস্তর নির্মিত-সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বাঁকুড়া জেলার দেউলভিড়্যার ল্যাটেরাইট পাহাড়ে তৈরি জৈন মন্দির, পুরুলিয়ার দেউলঘেরায় বান্দায় দেউল, পুরুলিয়ায় তেজকুপিয় মন্দিরগুলি।
- ভদ্র দেউল: এই রীতির মন্দিরে গর্ভগৃহের ছাদ পিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে যায়। ভূমি থেকে মন্দিরটি বাড়, ভদ্রগন্তি ও মস্তক তিন ভাবে বিভক্ত। ভূমি থেকে ‘বাড়’ অংশটি লম্ব ভাগে উপরে উঠলেও গন্ডি অংশটি পিরামিডাকৃতি গঠন যুক্ত। পিড়ি গুলি সামন্তরাল ও প্রান্তগুলি সরলরেখায় ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। এর উপরে অবস্থান করে মস্তক অংশ।
এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হল- বাঁকুড়া জেলার মনাপুরের হাকন্দ শিব মন্দির, খাতড়ার অতবাহচন্ডী শিব মন্দির।
মধ্যযুগের স্থাপত্য:
মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বখতিয়ার খলজির আক্রমনে লক্ষণাবতীর পতনের মাধ্যমে বাংলার মধ্যযুগের সূচনা হয়। প্রথম দিকের তুর্কি আক্রমণে প্রাচীন রীতির বৃহৎ দেউলগুলির বেশীর ভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সময় স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের সময় ভারতীয় পরম্পরার সাথে মুসলিম ধারার মেলবন্ধনে ‘ইন্দো-মুসলিম’ রীতির বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্য ও মুসলিম স্থাপত্যের বর্ণনা দেওয়া হল
মন্দির স্থাপত্য: সুলতানি আক্রমণে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের বড় বড় রেখ মন্দিরগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মালভূমি অঞ্চল সরাসরি মুসলিম আধিপত্যের বাইরে থাকায় স্থানীয় ভাবে কম উচ্চতাযুক্ত পরিবর্তিত রেখ দেউল তৈরি কিছুকাল বর্তমান ছিল।
গাঙ্গেয় সমভূমিতে বড় দেউলগুলি ধ্বংস হলে কুঠির আকারে লোকায়ত স্থাপত্য রীতিতে তৈরী মাটির চালাঘরে দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে চালা ঘরের আদলে ইটের স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা হয়। চালা মন্দির গুলি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রকার ও বৈচিত্র্যময়। যেমন-দো-চালা বা এক বাংলা মন্দির, দুটি চালা বা জোর বাংলা মন্দির, চারচালা, আটচালা ইত্যাদি। এই সময় ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির অনুসারী চালা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করা হল রত্ন বা রত্নরূপ শিখর। শিখরের এই রত্নগুলির চূড়ার সংখ্যার উপর একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন মন্দির নামে পরিচিতি লাভ করে।
উদাহরণ: মন্দির শহর বিষ্ণুপুরের মন্দির গুলিতে মধ্যযুগের চালা ও রত্নরীতির নিদের্শন পাওয়া যায়।
মুসলিম স্থাপত্য: সেন বংশের পতনের পর বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় ও ব্রিটিশদের দ্বারা শাসন ক্ষমতা দখল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল বাংলায় সমাজ সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে ও স্থাপত্য রীতির বিভিন্ন যুগ লক্ষ্য করা যায়।
প্রাক্ মুঘল রীতি: সুলতানী শাসনের প্রথম ২০০ বৎসর বাংলা ছিল সরাসরি তুর্কি সুলতানের অধীনে। এই সময় প্রাচীন বড় বড় হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির গুলিকে ধ্বংস করা হয় ও আদি গঠনে ব্যবহৃত পাথর ও ইটের দ্বারাই নতুন করে মসজিদ, দুর্গ ও সমাধিস্থল তৈরি করা হয়। এই সময়ের তুর্কি রীতির নিদর্শন হুগলীর ত্রিবেনীর জায়ার খান গাজীর সমাধিস্থল ও মসজিদ।
এই পর্যায়ে দিল্লির শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ইলিয়াস শাহী শাসকরা স্থায়ী রাজত্ব শুরু করে। এই সময় মুসলিম স্থাপত্য রীতির সাথে বাংলার স্থানীয় রীতির মেলবন্ধন শুরু হয়। মালদার আদিনা মসজিদ অন্যতম উদাহরণ।
হুসেন শাহীদের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অন্য মাত্রায় পৌঁছায় ও বাংলার শিল্প স্থাপত্য, ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। এই সময়ে ইটের তৈরি খিলান যুক্ত স্থাপত্য গুলি হল নট্রিন মসজিদ ইট ও পাথরের তৈরি স্থাপত্য এর মধ্যে অন্যতম হল বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ।
মুঘল রীতি: ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলায় বহুকাল রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় ছিল। এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার তিনটি স্থানে স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়। পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদ, পুরাতন মালদার কাটরাগেট, জামে মসজিদ ও নিমসরাই মিনার এবং শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ, বিবি মসজিদ ইত্যাদি।
বাংলায় মুঘল শাসনে স্থায়িত্ব আসার পর রাজধানী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে স্থাপত্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার চৌরিহাটা মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ ও ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দ্বিতীয় ভাগ। মুর্শিদাবাদে ইউরোপীয় শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যতম স্থাপত্য হল কাটরা মসজিদ, মোতিঝিল, হাজারদুয়ারি ইত্যাদি।
আধুনিক যুগের স্থাপত্য:
মুঘল আমলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য একে একে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় পদাপর্ণ ঘটে। প্রাথমিক ভাবে তারা কাশিমবাজারে গেলেও ব্যবসা ও বন্দরের নৈকট্যের জন্য সপ্তগ্রাম থেকে কলকাতার মধ্যে বাণিজ্য কুটি, প্রাসাদ, চার্চ, নির্মাণ করে। তৎকালীন অভিজ্ঞ স্থানীয়রা ইউরোপীয় রীতিতেই প্রাসাদ তৈরি করে। এই সকল নিদর্শন বর্তমানেও গোথিক, পর্তুগিজ, ফরাসী, আিেনীয ইত্যাদি ইউরোপিয় স্থাপত্য রীতির ধারক।
ফরাসী স্থাপত্য: ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে ইন্দো-ফরাসী-স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ফরাসি সরকার দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যগুলির বাইরের অংশবিশুদ্ধ ইউরোপীয় রীতি মনে হলেও অলঙ্করণে স্থানীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় অভিজাত দ্বারা নির্মিত প্রাসাদগুলিও ইন্দো-ফরাসী স্থাপত্যের পরিচয় বহন করে।
গোথিক স্থাপত্য: ইউরোপে নবজাগরণের ফলস্বরূপ এই গোথিক স্থাপত্য-এর উদ্ভব হয়। এই স্থাপত্য উঁচু উঁচু স্তম্ভের উপর মুকুট সদৃশ্য খিলানগুলি (Pointed Arch) সুসজ্জিত থাকে ও বৃহৎ কাঁচের জানলা লক্ষ্য করা যায়। কলকাতায় গোথিক স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ হল সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল।
ইন্দো-সারসেনিক স্থাপত্য: ভারতীয় প্রচলিত স্থাপত্যরীতি, ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য রীতি ও গোথিক স্থাপত্য রীতির মিশ্রনে ব্রিটিশ স্থাপত্যকারগণ এই রীতি প্রচলন করেন। স্থাপত্য রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পেয়াজ এর কন্দের মতো গম্বুজ, উঁচু উঁচু স্তম্ভ ও মিনার, হারেম বা ছোট ছোট জানলা, মুকট ও খাজযুক্ত খিলান ইত্যাদি। উদাহরণ: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, GPO অফিস, কলকাতা হাইকোর্ট ইত্যাদি।
বাংলার ভাস্কর্য:
পাথরের উপর খোদাই করে মূর্তি নির্মাণের প্রচলন এই বাংলায় প্রাচীন কাল থেকে চলছে। বিহার, মঠ ও মন্দির গ্রাহে এই রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাস্কর্য তৎকালীন শিল্পসত্বার পরিচয় বহন করে। গ্রীক আগমনের পর উত্তর ভারতের মতো বাংলার ভাস্কর্যও প্রভাবিত হয় ও তা মৌর্য, গুপ্ত ও পাল যুগে স্বমহিমায় বিকশিত হয়। ইসলাম আগমনের পর ভাস্কর্যরীতির অবলুপ্তি ঘটে। সুলতানি শাসনের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় সহজলভ্য নরম পলি মৃত্তিকার দ্বারা টেরাকোটার ভাস্কর্য প্রাধান্য পায়। কালের বিবর্তনে বাংলার পাথরের ভাস্কর্য ও টেরাকোটা শিল্পের বর্ণনা করা হল।
গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগ: কুষাণযুগের সমসাময়িক ভাস্কর্য এর ধ্বংসাবশেষ বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এই ভাস্কর্যগুলিতে মথুরা শিল্প রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিন ২৪ পরগণার চক্রকেতুগড় স্তূপ থেকে বেলেপাথরের বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির দুই হাতের নীচের অংশ ধ্বংস হলেও বস্ত্র আচ্ছাদিত বাম কাঁধ ও ধরের অংশ বর্তমান।
বরেন্দ্রভূমির হাকরাইল থেকে প্রাপ্ত চার হাত যুক্ত বিষ্ণুর গদা যুক্ত বেলেপাথরের মূর্তিতে মাথার পিছনে পদ্মের অবস্থান ও বস্ত্র পরিধান সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
গুপ্তযুগ: কুষাণযুগের ভাস্কর্য শৈলী এই সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। মূর্তিগুলির সুষ্ঠু পরিমার্জনা ও আধ্যাত্মিক রূপ সেই পরিচয় বহন করে। এই যুগের ভাস্কর্যগুলি আবেগপূর্ণ ও সংবেদনশীল। রাজধানীতে প্রাপ্ত চুনার বেলেপাথর দ্বারা নির্মিত গৌতমবুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তির চোখের পাশে, নাক ও মুখের ছায়ার মাধ্যমে দুঃখের আবেশ বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা কাশীপুর এর বৌদ্ধ মূর্তিতে একইরকম আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।
গুপ্তযুগের ধাতব ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হল মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের তৈরি ‘মঞ্জুশ্রী’ ভাস্কর্য মূর্তি। সোনার রঙ করা এই মূর্তিটিতে গৌতমবুদ্ধ আশীর্বাদ মুদ্রায় অবস্থানরত।
পাল ও সেনযুগের ভাস্কর্য: গুপ্তযুগের পর বাংলায় ভাস্কর্য সৃষ্টির ধারা পুনরায় গতি পায় পালযুগ। এই সময় ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সুনাম অর্জন করেন বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলের বিটপাল ও তার পুত্র ধীমান। দুজনেই ভাস্কর্য ও ধাতুমূর্তি গঠনে পারদর্শী ছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে তারা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পূর্বরীতির পথপ্রদর্শক ছিলেন। এই যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজশাহীর পাহাড়পুরের বৃহৎ মন্দির ও তৎসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ।
এই স্থানে প্রাপ্ত ভাস্কর্যগুলি বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয় ফলে ভাস্কর্যের গঠনরীতি সহজেই ভিন্ন করা যায়।
- প্রথম শ্রেণী: এই ধারায় ভাস্কর্যে ভারী অলঙ্কার এবং সুন্দর দৈহিক বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। রাধাকৃষ্ণ, যমুনা ও শিবের ভাস্কর্য বিখ্যাত।
- দ্বিতীয় শ্রেণী: এই ধারার ভাস্কর্যগুলির দৈহিক গঠন মোটা এবং মূর্তিগুলি অবসন্ন প্রকৃতির। কৃষ্ণ ও বলরাম এর মূর্তি অন্যতম।
- তৃতীয় শ্রেণী: ভাস্কর্যের দৈহিক গঠন অমসৃণ ও অপরিশোধিত। কৃষ্ণের জীবনচিত্র বর্ণনা এই ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে।
বাংলার টেরাকোটা: নরম ও সহজলভ্য মাটিতে ভাস্কর্য তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে পোড়ানো হয়। মৌর্য-গুপ্ত যুগে টেরাকোটা ভাস্কর্য তৈরির প্রচলন থাকলেও পালযুগে এই শিল্প বিকাশ লাভ করে। প্রাচীন মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত টেরাকোটা স্থাপত্য গুলি সেই পরিচয় বহন করে। মুসলিম শাসনের মধ্যভাগে বাংলার চালা ও রত্ন মন্দির গুলির বর্হিদেশ ও অভ্যন্তরের সজ্জা সম্পন্ন করা হতো এই টেরাকোটা ভাস্কর্যের মাধ্যমেই। টেরাকোটা শিল্পীরা ধর্মীয় প্রেরণামূলক চিত্রের সাথে সমকালীন বহু সমাজচিত্রও রূপায়িত করেছেন বাংলার মন্দিরগুলির দেওয়ালে। চন্দ্রকেতুগড়, ভিতরগাঁও ইত্যাদি স্থানে গুপ্তযুগের টেরাকোটা স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পালযুগে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ইত্যাদি বৌদ্ধস্তূপে টেরাকোটা অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। পালযুগের প্রথমপর্বের টেরাকোটাগুলিতে নরনারী, দেবদেবী ও পশুপাখির ভাস্কর্য থাকলেও দ্বিতীয় পর্বে কীর্তিমুখ, চৈত্য, গবাক্ষ ও নানা প্রকার জ্যামিতিক নকশার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্য পরবর্তী যুগে বাংলায় পুনরায় টেরাকোটা ব্যবহারে জোয়ার আসে। নব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় বাংলায় অগণিত ইটের মন্দির তৈরি হয় ও সেগুলি সুসজ্জিত হয় টেরাকোটা অলঙ্করণে।
মৃৎপাত্র: বাংলায় মৃৎপাত্র তৈরির ইতিহাস 3000 বৎসর পুরোনো যা তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে। হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বর্ধমানের পান্ডুরাজার ঢিবিতে মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই স্থানে প্রথম ভাগে তাম্রপ্রস্তর যুগের লালবর্ণের পাত্র পাওয়া গেছে। এই পাত্রের উপরিভাগে কালো রঙের ত্রিভুজ ও চতুষ্কোনাকার নক্সার চিত্রায়ন লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে প্রাক্ ঐতিহাসিক কালো ও লাল রঙের পাত্রের (Protohistory Black & Red ware) অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। উত্তর ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় থেকে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের মৃৎপাত্র এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই স্থানে প্রাপ্ত কালোরঙের পালিশযুক্ত পাত্রগুলির সুসজ্জিত রূপ বানগড় ও মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পাত্রের ন্যায়। এই শ্রেণীকে নর্দান ব্লাক পলিসড ওয়ার বলা হয়। এই পাত্রগুলিতে উপকূলবর্তী অঞ্চলের চিত্র এবং গ্রিক-রোমান শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় ভাগের কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্রের ওপর ধূসর সাদা বর্ণের জালের সংলগ্ন একসারি মাছ এবং অন্য একটি পাত্রে একটি ময়ূরী ঠোট দিয়ে একটা সাপ ধরে আছে। তৎকালীন বাংলার মানুষের রসনাতৃপ্তিতে মাছের প্রাধান্যকে বর্ণনা করে।
বাংলার চিত্রকলা:
বাংলার চিত্রকলার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও এর আদি নিদর্শন স্বল্প। পাল রাজত্বকালে নালন্দা মহাবিহারে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের রঙিন পাণ্ডুলিপিগুলিই হল বাংলার প্রাচীনতম চিত্রকলার নিদর্শন। এই পরিণত চিত্রকলার নিদর্শন দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, বাঙালী চিত্রশিল্পীদের দীর্ঘদিনের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলেই এই চিত্র সম্ভব রয়েছে। কিন্তু বলের বিবর্তনে পূর্বের চিত্রকলার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় কিন্তু হুসেনশাহীরাজত্বকালে পুনরায় চিত্রকলার নবরূপে পথ চলা শুরু হয় ও চৈতন্যদেব আগমনের পর এর গতি তরান্বিত হয়। মুঘল আমলে মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদশৈলী জনপ্রিয় হয়। ইউরোপীয় চিত্র শিল্পদের পাশাপাশি বাঙালী চিত্রশিল্পীরা নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি করে বাংলার চিত্রকলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে। পাল যুগ থেকে বাংলার চিত্রকলার ক্রমান্বয়িক বিকাশ বর্ণনা করা হল-
পালযুগের চিত্রকলা:
পালযুগের চিত্রশিল্পীরা মাগধী রীতি বা ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল রীতির প্রবাহমান ধারাকে অনুসরণ করেছিলেন। লামা তারানাথের বর্ণনা থেকে বাংলার বিখ্যাত ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পী পিতা-পুত্র বিটপাল ও ধীমান এর পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিটপাল পূর্বদেশীয় রীতি গ্রহন করেন এবং ধীমান ‘মাগবী রীতি’ গ্রহন করেন। পালযুগে চিত্রঅঙ্কন করা হতো তালপাতায়। ভারতীয় চিত্রকলার নিয়মে কালো বা লাল সূক্ষ তুলিতে প্রবাহমান তরঙ্গের দ্বারা দেহ কাঠামো ও করাহলির বহিরেখা টানা হতো। এই যুগের চিত্রের অন্যতম বিষয় হল গৌতমবুদ্ধের জীবনচক্র এর বর্ণনা, এছাড়াও তান্ত্রিক দেবদেবীদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, লোকনাথ, মৈত্রেয়, বজ্রপানি, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীদেব প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
সুলতানি শাসন ও চিত্রকলা:
মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের সংঘাত ও বিরোধ এর পর ইলিয়াসশাহের সময় থেকে বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় সুলতানেরা ইসলামে পূর্ণবিশ্বাসী থেকেও বাংলার দেশজ সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। এই পৃষ্ঠপোষকতা হুসেন শাহীদের সময় আরও ব্যাপ্তিলাভ করে। নসরৎ শাহের সময় রাজসভায় পারসিক চিত্রশিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। জনমানসে বৈষ্ণব ধর্মচারণের ফল স্বরূপ নবদ্বীপ ও বিষ্ণুপুর বাংলার স্থাপত্য ও চিত্রকলার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার পাটা চিত্রশৈলী নিকটবর্তী অঞ্চলে – ছড়িয়ে পড়ে। পাটা চিত্রের প্রধান বিষয় বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী হলেও অন্য – সম্প্রদায়ের রুপভাবনাও প্রতিফলিত হয়েছে।
মুর্শিদাবাদ শৈলী:
নবাব মুর্শিদকুলির সময় মহরম উপলক্ষে নগর সজ্জায় প্রচুর চিত্রশিল্পীর আগমন ঘটে। 1720 সালে অঙ্কিত মহরম উৎস এ বর্ণনার চিত্র মুর্শিদাবাদ শ্রেণীর আদি নিদর্শন। আলিবর্দির সময় মুর্শিদাবাদ – শৈলীর প্রকৃত বিকাশ হয়। এই সময়ের নবাবের শিকার যাত্রা, রাজসভার সুন্দর চিত্রায়ন রয়েছে পাণ্ডুলিপিগুলিতে। সিরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা নতুন রূপ বিন্যাসে আঁকলেন বাগমালা সিরিজের ছবি। হিন্দু অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু পৌরানিক কাহিনী, শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণের চিত্রায়ণত ই হয়েছে।
কোম্পানী চিত্রকলা:
কলকাতা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়ার র পর অর্থ উপার্জনের জন্য ইউরোপীয় শিল্পীরা বাংলায় পদার্পণ করেন। প্রাথমিক ভয় সময়ে যারা পদার্পণ করেন সেই শিল্পীরা তেল রঙে প্রতিকৃতি, মজলিস ও ভর ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কন করতেন। চিলি বেইল, জোফানি ডেভিস, হিকি প্রমুখ বিখ্যাত। এই সময়ে আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলি হল- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল রক্ষিত ‘যীশুর শেষ ভোজ’ হায়দার বেগের দৌত্য, টিপুর পুত্রকে কর্ণওয়ালিসের জমিন রূপে গ্রহণ। পরবর্তী সময় শিল্পীরা এঁকে গেছেন ব্রিটিশ পরম্পরার স্বচ্ছ জলরঙের ছবি যা বর্ণনা করছে স্থানীয় মানুষের জীবন চিত্র।
পটচিত্র ধারা:
সংস্কৃত পট কথাটির অর্থ ‘কাপড়’। কাপড়ের ফালির ওপর আঁকা হয় ও কাঠের একটি দন্ডে জড়ানো হয় পটচিত্র। জনপ্রিয় জড়ানো পট ছাড়াও চৌকস্ পটএর প্রচলন ছিল প্রাচীন সময় থেকেই। পটুয়ারা একই সাথে চিত্রকার এবং কবি, গীতিকার ও সুরকারও। পট দেখিয়ে গান গেয়ে লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জন করে এসেছেন। রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ, ভগবত পুরাণ, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্য জীবন অবলম্বনে অঙ্কিত পট প্রাধান্য পেয়েছে। অবস্থান ও স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী পটচিত্র ও শৈলীতে ভিন্নতা ঘটেছে। বৈচিত্র অনুসারে বাংলার পটচিত্রকে চার ভাগে ভাগ করা যায় (1) সাঁওতাল উপজাতীয় জীবন (2) যমপট ও হিন্দু পুরাণ (রামায়ন-মহাভারত) (3) চৈতন্য পটভূমি (4) গাজীপট।
কালীঘাট পটশৈলী:
বাঙালীর পটচিত্রের পরম্পরা অন্য উচ্চতায় পৌঁছায় কালিঘাটের পটচিত্র। বাঙালীর নিজস্ব শিল্প অভিব্যক্তি। কালীঘাটের পটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে গৌরব অর্জন করেছে। রেখার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মাধ্যমে রূপের গড়নকে ফুটিয়ে স্বচ্ছ ও সুমিত বিন্যাসের মাধ্যমে গড়নকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে পটুয়ারা। কালীমন্দির ঘিরেই এই পটচিত্রের বিকাশ ঘটে ফলতই প্রধান বিষয় ছিল কালী ও অন্যান্য দেবদেবী। পরবর্তীকালে সমকালীন জীবনের চিত্রও তুলে ধরা হয়।
নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার বিকাশ: অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর:
1858 সালে স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চার দশক ধরে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ইউরোপীয় শিল্প রীতিতে শিক্ষিত করে তোলা। ব্লুমফিল্ড হ্যাভেল আর্ট স্কুলের দায়িত্ব নেবার পর প্রাচ্যের চারু ও কারুকলার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুত্থানে হ্যাভেল এর অহ্বানেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1905 সালে আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাথমিক ভাবে ইউরোপীয় ধারায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষা লাভকরেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্রের রীতির দিকে আকৃষ্ট হন ও রবীন্দ্রনাথের উপদেশে বৈষ্ণব পদাবলীর অবলম্বনে ‘কৃষ্ণলীলা সিরিজ’ এর চিত্র এঁকে ভারতীয় চিত্রকলার নব যুগের সৃষ্টি করেন। তবে নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতি স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। অভিসারিকা, বুদ্ধ ও সুজাতা, পদ্মাবতী ও বেতালপঞ্চবিংশতি অন্তিম শয্যায় শাহজাহান উল্লেখযোগ্য। তার নব্য-বঙ্গীয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ।
আধুনিকতার প্রবর্তন: গগনেন্দ্রনাথ যামিনী রায়-রবীন্দ্রনাথ:
স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা বিকাশ লাভ করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারনা চিত্রকলাকে প্রভাবিত করে ও চিত্রকলায় আধুনিকতায় সূত্রপাত করেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথ এর ওয়াশরীতিতে চিত্রাঙ্কন করলেও তার শিল্প প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ ঘটে ‘কিউবিষ্টধর্মী’ ছবিতে। আলো-ছায়া বৈচিত্র তিনি সাদা ও কালো রঙের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আলো-ছায়ায় খেলাকে সুন্দর রঙের মাধ্যমে বিচিত্র ভাবে রাজকন্যা, হিমালয়ের সংগীত, উচ্চহাস প্রভৃতি চিত্রে তুলে ধরেছেন। ইউরোপীয় চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহন করলেও যামিনী রায় আর্ট স্কুলে ফিরিয়ে আনেন। মাটির চালে তাঁর বাড়ি বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ো গ্রামীণ পরিবেশে, পটুয়াদের দেশীয় পদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন ফলে তার চিত্রশৈলীতে প্রাধান্য পেল, সাঁওতাল জীবনযাত্রা, চৈতন্যজীবন, কৃষ্ণ-রাধা ইত্যাদি।
যামিনী রায়ের পর আধুনিক বাংলার চিত্রকলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নূতন রূপ পায়। পান্ডুলিপির সংশোধনীর সময় তার কাটাকুটি ছবি হয়ে উঠেছিল প্রারম্ভিক পর্যায়ে। এরপর তিনি রেখা চিত্রের মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন করলেও1930 এরপর তার পরিণত পর্যায়ের চিত্রাঙ্কনের যাত্রা শুরু হয়। তার ছবিতে দেখা যায় ঘষে ঘষে গাঢ় জলরঙের ব্যবহার। এছাড়াও তিনি ত্রিমাত্রিক গড়নে মানবিক ও অমানবিক মুখমন্ডল অঙ্কন করেন যা আধুনিক চিত্রকলার সম্পদ।
বাংলার হস্তশিল্প:
প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিশ্বব্যাপী সামাদৃত হয়েছে। তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতু গড় ইত্যাদি বন্দর শহরের মাধ্যমে বণিকরা প্রচুর পরিমানে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করত তা বৈদেশিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। বাংলার রপ্তানীজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রাধান্য পেতে সিল্কজাত কাপড় ও টেরাকোটা। যুগের বিবর্তনে শাসক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হলেও বাংলার সুদক্ষ কারিগররা তাদের হস্তশিল্পের অনন্যতা বজায় রেখেছে। যা আজও বিশ্বব্যাপি সমাদৃত হয়ে চলেছে। নিম্নে জেলাভিত্তিক প্রধান প্রধান হস্তাশিল্পের বর্ণনা বাধ্য দেওয়া হল-
বাংলার সুদক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত 13টি হস্তশিল্পজাত সামগ্রী Geographical Indication (GI Tag) মর্যাদা লাভ করেছে। এই দ্রব্যগুলি বাংলার নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কাজ করে আসা দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি হয়ে চলেছে ও দ্রব্যগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম।
| ক্র. নং | নাম | GI প্রাপ্তি | অঞ্চল | দ্রব্যের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নকসি কাঁথা | ২০০৭ | গ্রামীণ বাংলা | গ্রাম বাংলার মহিলারা নক্সা সেলাইয়ের মাধ্যমে কাঁথা তৈরি করেন। বর্তমানে শাড়ি, পাঞ্জাবীতে বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। |
| ২ | শান্তিনিকেতনের চামড়ার হস্তশিল্প | ২০০৭ | শান্তিনিকেতন (বোলপুর) | চামড়ার তৈরি জুতো, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। |
| ৩ | বালুচরী শাড়ি | ২০১১ | বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া | সিল্কের শাড়িতে রামায়ণ, মহাভারত ও সামাজিক ঘটনার চিত্রায়ন দেখা যায়। |
| ৪ | বাঁকুড়ার টেরাকোটা ঘোড়া | ২০১৮ | বাঁকুড়া (পাঁচমুড়া, রাজগ্রাম, সোনামুখি) | টেরাকোটার ঘোড়া ও দেবদেবীর ভাস্কর্য তৈরি হয়। |
| ৫ | পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ | ২০১৮ | বাঘমুন্ডি, পুরুলিয়া | ছৌ নাচের জন্য মুখোশ; বর্তমানে ঘর সাজানোর কাজেও ব্যবহৃত। |
| ৬ | ধনিয়াখালি শাড়ি | ২০১১ | ধনিয়াখালি, হুগলি | সুন্দর নক্সাযুক্ত সুতির শাড়ি। |
| ৭ | ডোকরা শিল্প | ২০১৮ | বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান | ছাঁচের সাহায্যে ধাতব ঘোড়া, হাতি, ময়ূর, পেঁচা ইত্যাদি তৈরি হয়। |
| ৮ | গরদ শাড়ি | ২০২৪ | মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম | হাতে তৈরি শাড়ি; দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পূজায় ব্যবহৃত। |
| ৯ | কোরিয়াল শাড়ি | ২০২৪ | মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম | সাদা বা ধূসর-সাদা রঙের লাল পাড়যুক্ত ঐতিহ্যবাহী শাড়ি। |
| ১০ | মাদুর কাঠি | ২০১৮ | মেদিনীপুর | সাইপ্রাস ঘাস দিয়ে বংশপরম্পরায় মাদুর তৈরি করা হয়। |
| ১১ | পটচিত্র | ২০১৮ | গ্রামবাংলা | পটুয়ারা দেবদেবী ও সমাজজীবনের চিত্র পটে অঙ্কন করেন। |
| ১২ | শান্তিপুর শাড়ি | ২০০৯ | শান্তিপুর, নদীয়া | ঐতিহ্যবাহী সুতির শাড়ি। |
| ১৩ | কুশমান্ডির কাঠের মুখোশ | ২০১৮ | কুশমান্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর | পোমিরা নৃত্যের জন্য কাঠের মুখোশ তৈরি হয়। |
২০২৫ সালে নতুন জিআই ট্যাগ:
- নোলেন গুড়ের সন্দেশ: খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি একটি জনপ্রিয় শীতকালীন মিষ্টি।
- বারুইপুরের পেয়ারা: বারুইপুর অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট জাতের পেয়ারা.
- কামারপুকুরের সাদা বোঁদে: কামারপুকুরের একটি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি
- যার নাম বোঁদে।
- মুর্শিদাবাদের ছানাবরা: ছানা (কটেজ পনির) দিয়ে তৈরি একটি মিষ্টি।
- বিষ্ণুপুরের মতিচুর লাড্ডু: বিষ্ণুপুরের একটি নির্দিষ্ট ধরনের মতিচুর লাড্ডু।
- রাধুনীপাগল চাল: দক্ষিণবঙ্গের একটি সুগন্ধি ধানের জাত।
বাংলাগান:
পাল ও সেন রাজাদের সময় বাংলাভূমিতে এই অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য চর্চা হত অপভ্রংশ থেকেই বাংলার আদিরূপ এর জন্ম। সাধারণ লোক বৌদ্ধ ধর্মগুরু, শৈব নাথপন্থী ধর্মগুরুরা এই ভাষায় গান লিখতেন এবং তাদের গানগুলোই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা। বৌদ্ধ পন্ডিতরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থা বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, চর্যাগীতি বা চর্যাপদ এ বর্ণনা করে গেছেন। প্রত্যেক চর্যাপদে রাগরাগীনির উল্লেখ রয়েছে। যেমন পটমঞ্জরী, মল্লার, ভৈরবি ইত্যাদি। প্রত্যেক গানের ভনিতায় পদকর্তাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।
জয়দেবের ও বড়ু চণ্ডীদাস: বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে লক্ষ্মন সেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামী এক অন্যতম নাম। তাঁর রচিত গীত গোবিন্দ বাংলা ভূমিতে বৈষ্ণব গীতিকারিতার রসস্রোতকে বইয়ে দিয়েছিলেন। জয়দেব পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী নিয়ে গীত রচনা করেন বড়ু চন্ডীদাস। খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনায় এর কবিতা গুলি মূলত গাওয়ার জন্য লেখা হয়েছিলে কারন প্রতিটি গীতের শীর্ষে সুর তালাদির বর্ণনা রয়েছে।
যাত্রাগান ও পাঁচালী গান: ষোড়শ শতাব্দীর পর বাংলায় যাত্রার প্রচলন হয়। দেবপূজার উৎসব বা শোভাযাত্রা উপলক্ষে নাট্যগীত যা পরবর্তীতে যাত্রা গানে পূর্ণতা পায়। পাঁচজন দাঁড়িয়ে চামর হাতে যে ছন্দে গাঁথা গান গাওয়া হত তাকে পাঁচালি বলা হত। কৃত্তিবাসের রামায়ন পাঁচালী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাঁচালি গায়কদের নুপূর এবং হাতে চামর ও মন্দিরা থাকত। পাঁচালি কবিদের মধ্যে বিখ্যাতি ছিলেন দাশরথি রায়।
পদাবলি: মধ্যযুগে বাংলাদেশে সমাজ ধর্ম দুটি ধারা পাশাপাশি বর্তমান ছিল। একটি বৈষ্ণব ও অন্যটি শাক্ত ধারা।
বৈষ্ণব পদাবলী: বৈষ্ণব মতাদর্শের অনুসারীরা তাদের রচিত পদাবলীর মাধ্যমে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেছেন। এই পদাবলির মূল বিষয় বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম লিলা। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে চৈতন্য অবতার রুপে পূজিত, এই কারনে কবিরা রাধাকৃষ্ণের পাশাপাশি চৈতন্যদেবকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন।
(কীর্তন অর্থে খ্যাতি, মহিমা ও যশ সূচক গানকে বোঝায়। অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবতার গুণ-গাথা গান করা বা ‘কর্তন’ করার নামই কীর্তন। কীর্তনগুলি শাস্ত্রীয় রাগ ও তালে রচিত হলেও, এর গানের সুর-বিন্যাস রীতি সমস্ত প্রচলিত সংগীত রীতি থেকে স্বতন্ত্র। ভারতীয় সংগীতে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবদান হল কীর্তন)
শাক্ত পদাবলী: শাক্ত পদাবলির বিকাশ ঘটেছে উমা, পার্বতী, চন্ডী ও কালিকাকে কেন্দ্র করে। শাক্ত পদাবলি দুই প্রকারের ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত এবং আগমনী বা বিজয় গান। এই পদাবলীগুলিতে উমার পিতৃগৃহে আগমন ও পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামী গৃহে যাত্রা প্রসঙ্গে মা মেনকার হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।
রামপ্রসাদ: শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। হালিশহরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি তান্ত্রিক মতে কালী সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ আধ্যাত্মিকতা, সমাজ এবং বাস্তব কাব্য রসের ত্রিবেদী রচনা করে ভক্তিগীতি সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দেন। তার গানে সমসাময়িক সাধারণ মানুষের দুখ, দুর্দশারও বর্ণনা করেছেন। তিনি উমা, তান্ত্রিক ও তত্ত্বদর্শন বিষয়ক গান রচনা করেছেন।
দেশাত্মবোধক গান: গ্রাম বাংলার সামাজিক সমস্যা-সমাধান ফুটে উঠতো লোক সংগীতের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন জাতীর আশা, আকাঙ্খা ও মুক্তির সংগ্রামের ভাষা যে সংগীতের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাদের জাতীয় সংগীত বা স্বদেশী গান বলা হত। দেশাত্মবোধক গানে কেউ অতীত গৌরব তুলে ধরেছেন, কেউ স্বদেশের গুণাগুণ করেছেন, কেউ গানের দ্বারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে প্রতিবাদ করতে বলেছেন। গায়কদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মুকুন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলাম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ।
খেয়াল: অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বহু খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা গানে খেয়ালের প্রচলন শুরু হয়। খেয়াল গানের পথিকৃত ছিলেন যদু ভট্ট। রামমোহন রায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। খেয়াল মুক্ত প্রকৃতির গান রাগ বিস্তার ও অলঙ্করনের ক্ষেত্রে গানে স্বাধীনতা অনেক বেশী।
টপ্পা অঙ্গের গান: টপ্পা হল সংক্ষিপ্ত গান। ত্রিবেনীর রামনিধি গুপ্ত শোরী মিঞার টপ্পার রাগ, তাল ও রীতি অনুসরণ করে প্রথম বাংলা গানে এই রীতি প্রচলন করেন। বহুদেশে গুপ্তিপাড়ার কালী মির্জা টপ্পা রচয়িতা হিসেবে পরিচিত লাভ করেন।
ঠুংরী অঙ্গের গান: বাংলায় ঠুংরী রীতির প্রবর্তন ওয়াজেদ আলী শাহ। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় নির্বাসিত হয়ে মেঠিয়াপুকুর দরবারে ঠুংরী চর্চা অব্যাহত রাখেন। আধুনিক ঠুংরী এই অঞ্চলে জনপ্রিয় করেন গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী। রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ঠুংরী গান রচনা করেন।
অতুলপ্রসাদ সেন: 1871 সালে ঢাকাতে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বাংলায় আধুনিক রাগ প্রধান গানের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। তাঁর টপ্পা-ঢংয়ের গানগুলি অধিকাংশ করুন রসের। স্বদেশী গানের তিনি অতীত গৌরব বোধ, ভৌগোলিক বিবরণের মাধ্যমে জনমানসে উত্তেজনা সঞ্চার করেছিলেন। তার স্বদেশী গানেও বিদেশী সুরের মিশ্রন লক্ষ্য করা যায়।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়: কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 1663 সালে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহন করেন। তার স্বদেশীগান বাংলার অমূল্য সম্পদ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সাথে তার পরিচিতির প্রকাশ পায় স্বদেশীগানের মাধ্যমেই। কাব্য সাহিত্যে, প্রেম সংগীত ও ভক্তিমূলক সংগীতে ও তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।
কাজী নজরুল ইসলাম: 1899 সালে চুরুলিয়ায় তিনি জন্মগ্রহন করেন। ভারতীয় সংগীতের প্রায় সবকটি রীতিতেই তিনি গান রচনা করেছেন। ধ্রুপদ,খেয়াল, ঠুংরী, রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ইসলামী সংগীত, শ্যামা সংগীত, সব রীতিতেই নজরুল গীতি রয়েছে। তিনি একই সাথে গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। ভারতীয় রাগরাগীনির মিশ্রনে, লোকসঙ্গীতে বাংলা গানে আরবী ও পারসী সুরারোপে তিনি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা বাঙালীর দ্বারা চিরসমাদৃত হবে।
বাংলার লোক সংগীত:
লোকসঙ্গীত নামটিই সূচিত করে লোকের দ্বারা সৃষ্টি করা বা লোকের দ্বারা গাওয়া গানকে লোক সঙ্গীত বলে। লোক কথাটি ইংরেজী Folk এর প্রতিশব্দ। সাধারণ ভাবে গ্রাম্য চাষী, শ্রমিক, মজুর, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের যুগের পর যুগ ধরে যে গান সৃষ্টি করে চলেছে সেগুল্টি লোকসংগীত। সাধারণ মানুষ তিনটি কারনে গান করে-দেবতার উদ্দেশ্যে, কাছের অন্য মানুষকে শোনানোর জন্য, তার নিজের মনকে মানানোর জন্য। প্রাথমিকভাবে দেবতার উদ্দেশ্যেই লোকসংগীত শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে সমাজ জীবনের সাথে গানের ভার মিলিত হয়। বাংলায় প্রচলিত লোকসঙ্গীতগুলির বিবরণ দেওয়া হল-
বাউল: পল্লী বাংলার মানুষেরা বাউল জীবনদর্শে বিলীন করে দিয়েছে। বাউল জীবনাদর্শই হল মানব প্রেমের এক অভিনব এবং সার্থক প্রচেষ্টা। তাদের পোশাক পরিচ্ছন্ন, গানের কথা ও সুর, আচার প্রণালী এবং আধ্যাত্মবাদ ও দর্শন সবই বাংলার বহুরুপী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রকাশ। বাউলেরা মানুষের পূজারী। তাদের ধর্ম হল মানব ধর্ম, তাই তারা জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ বিরোধী। তাদের বিশ্বাস মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ার লালন ফকিরকে বাউলের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বলা হয়। তিনি অসাধ্য বাউল গান রচনা করে গেছে। বর্তমানে পূর্ণদাস বাউল, শক্তিপদ বাউল উজ্জ্বল প্রতিভা।
ভাওয়াইয়া: উত্তর বাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, অসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, এই কীর্তন অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষাও আঞ্চলিক সুরে এক বিশেষ ঢঙে গলার স্বরকে ভেঙে দিয়ে এই গান গাওয়া হয় স্থানীয় কোচ, মেচ, পলিরা উপজাতিদের দ্বারা। দোতারাই হল এর একমাত্র আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র। ‘ভাব’ কথাটি থেকে এই ভাওয়াইয়া শব্দে উৎপত্তি। আব্বাসউদ্দিন, শিবেন মন্ডল, পারুলবালা, প্যারীমোহন দাস প্রমুখ ছিলেন ভাওয়াইয়ার শিল্পী।
ভাটিয়ালী: পূর্ব বাংলার ঢাকা, ময়মনসিং ফরিদপুর অঞ্চলের মাঝিদের কণ্ঠে শোনা যায় এই মনমাতানো ভাটিয়ালী গান। ভাটা শব্দ থেকে ভাটিয়ালির উৎপত্তি। ভাটার টানে নৌকায় বসে খাল, বিল, নদী জলাশয়ে ভরা এই বাংলার মনমাতানো এই গান মাঝিদের কন্ঠে প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।
গম্ভীরা: পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার প্রধান লোক উৎসব হল গম্ভীরা। ‘গম্ভীর’ শব্দ থেকেই গম্ভীরার উৎপত্তি। গম্ভীর হলেন শিব। গম্ভীর অর্থে শান্ত, ধীর স্থির। হিন্দুধর্মের পুনরুস্থানের সময় রুদ্র মুর্তি শিব মূত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছ। এই উৎসবে শিব বন্দনা হলেও ভক্তি ছাড়াও সমাজনীতি, রাজনীতি, সুখ-দুখ ইত্যাদির কথা শোনা যায়।
টুসু পরব ও গান: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের মেয়েরা শষ্যের দেবী ‘টুসু’এর পূজা করে ও আনন্দ উৎসবে নাচ গানে মেতে ওঠে। পৌষ মাস ধরে টুসু গানে মেতে ওঠে এবং সংক্রান্তির টুসু ভাসান এর বিশেষ ধরনের ‘ছড়াকাটা’ সুর দিয়ে গান ধরে ও সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে থাকে।
ঝুমুর: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদেপ্রচলিত। বাংলার ঝুমুর গান রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা উপলক্ষেই শোনা যেত। অনেকের মতে ঝুমুরের উৎপত্তি সাঁওতালী গান থেকে। আদিবাসীরা বাঁশী ও মাদল বাজিয়ে নৃত্য সহযোগে তাদের আঞ্চলিক ভাষায় ও সুরে রচিত ঝুমুর গান ও প্রচলিত। সাঁওতাল ঝুমুর আয়তনে ছোট হয় অন্যদিকে মানভূমের ঝুমুর বেশ বড়।
ভাদু গান: ভাদ্র মাসের প্রথমদিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত, মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে ভাদু বা ভদ্রেশ্বরীর একটি মূর্তি গড়ে পূজো করে, নাচ, গানে ভারপুর এই লোক উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলায় মালভূমি অঞ্চলে অবিবাহিতা ‘ভাদু’ বিয়ের কথার বর্ণনা নিয়েই গানগুলি গাওয়া হয়।
রবীন্দ্রসংগীত: বাংলা তথা ভারতের সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক জীবনে সংগীতকে যে গভীর মূল্যদান করেছেন তা তাঁর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়- ‘আমি যখন গান বাঁধি, তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই’। তিনি একবার লিখেছিলেন-
‘যবে কাজ করি, প্রভু দেয় মোরে মান।’
যবে গান করি, ভালোবেসে ভগবান।’
সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ ‘সংগীত ও ভাব’-এ গানের কাথাকে সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করার বর্ণনা করেন। কবি সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা গ্রন্থে সংগীতে সুরের মাধ্যমে প্রাণের সঞ্চারের উপযোগিতা বর্ণনা করেন। ‘সংগীত ও কবিতা’ প্রবন্ধে তিনি কথা ও ভাবের মিশ্রন নিয়ে গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। ‘গীতবিতান’ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের গানগুলিকে কবি স্বয়ং বিষয়ানুসারে সুবিন্যস্ত করে পাঠকদের কাছে প্রেরণ করেন। গীতবিতানের গানগুলিকে কবি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যেমন ‘পূজা’, ‘স্বদেশ’, ‘প্রেম’, ‘প্রকৃতি’, ‘আনুষ্ঠানিক’ এবং ‘বিচিত্র’। ঈশ্বর মানব ও নিসর্গ এই তিন সাম্রাজ্যেই কবির বিচরণ ক্ষেত্র। তাঁর গানগুলিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-
- নাট্যগীত: রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সুবিপুল এবং জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই কবি নাটককে গীতস্নিগ্ধ করার জন্য সংগীতের অকৃপন ব্যবহার করেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক সাংকেতিক, প্রহসনাত্মক নাট্য, সামাজিক নাট্য বিভিন্ন বিভাগে তার নাট্যগীতের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ঋতু ও প্রকৃতির গান: তাঁর সম্পাদিত গীতবিতানেই প্রকৃতি ও ঋতু পর্যায়ের গীত সংখ্যা ২৮৩। ঋতু প্রকৃতির গানগুলিতে নিসর্গ জীবনের বিচিত্র রূপ যেমন মনোহর ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি সুরের দিক থেকেও গানগুলি সহজ প্রাণস্পর্শী। বৈশাখ থেকে চৈত্র-বারো মাসের ছয় ঋতুর বৈচিত্র তিনি বর্ণনা করেছেন।
- প্রেমপর্যায় গান: তার গানে দেবতা ও মানব এক চৈতন্য ভূমিতে মিলিত হয়েছে। কবিকাহিনী, বনফুল, নলিনী, মানসী, নৈশসংগীত, সান্ধ্যসংগীত ইত্যাদি কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমময় ও ভালবাসায় অমৃতময়।
- পূজাপর্যায়: গীতবিতানের প্রথম খন্ডে পূজাপর্যায়ে ৬১৭টি গান সংকলিত হয়েছে। ঈশ্বর মানব এবং প্রকৃতি এই তিন জগতে বিরাজমান রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সর্বাধিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তার সংগীতের মাধ্যমে।
- স্বদেশ পর্যায়: তাঁর দেশাত্মবোধক গানের সাথে বাংলার জাতীয় আন্দোলন অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই সর্বপ্রথম কবিকে প্রদীপ্ত জনসংগীতও জাতীয় সংগীত রচনায় বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে ও স্বদেশ পর্বের গানগুলি মাতৃভূমির প্রতি কবিমনের অকৃত্রিম মহত্ব প্রকাশিত হয়েছে।। বিষ্ণুপুর ঘরানা: বাংলার একমাত্র শাস্ত্রীয় ঘরানা লালিত ও সমৃদ্ধ হয় ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দরবারে। বিষ্ণুপুর ছিল বৈষ্ণব ধর্মাচার্যদের কাছে পূণ্যভূমি ফলে পদাবলী কীর্তন ও লোকগীতিময় ছিল মল্লরাজধানী। মল্লরাজা এ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজসভায় মুঘলদরবারের বাহাদুর খান এবং স্থানীয় নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির ও গদাধর চক্রবর্তীর সুরের মিশ্রনে এই । বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব হয়। বাহাদুর খানের পর মল্লরাজার সভার গায়ক হন ন গদাধর চক্রবর্তী। তাঁর পরিবারে অনন্তলাল চক্রবর্তীসহ অন্যান্য সদস্য এই । ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই শাস্ত্রীয় ঘরানার অন্যান্য গায়ক ছিলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী প্রমুখ।
বাংলার নৃত্যঃ
বাংলার লোকনৃত্যের ধারাটি অতীব সুপ্রাচীন। লোকায়ত – জীবনবোধ থেকে স্বতোৎসারিত সুর ও ছন্দ তাঁর আপন মহিমায় বিস্তৃত হয়েছে বাংলার লোকসৃষ্টির মহাঅঙ্গনে। বাংলায় শ্যামল সরস প্রাকৃতিক অবদান বাংলার লোকনৃত্যের অন্যতম আবহ উপাদান। বাংলার লোকনৃত্য ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হল।-
- ধামাইল: শ্রীহট্ট জেলার ধামাইল গানের সাথে বৌ-নাচ অবিভক্ত বাংলার এক বহুল প্রচলিত নৃত্য। কুমারী মেয়েরা ঘুরে ঘুরে এক বিশেষ ভঙ্গিতে এই নাচ পরিবেশন করে থাকে।
- জারি নৃত্য: জারি শব্দের অর্থ রোদন বা কান্না। কারবালার হাসান – হুসেনের ঘটনা জারিগান বর্ণনা করা হয়। একদল ছেলেরা তাজিয়া নিয়ে নীরব – হয়ে মিছিল করে, অন্যদল তরবারি নিয়ে যুদ্ধের কৌশলে নৃত্য পরিবেশন করে – থাকে।
- ঘাটু নৃত্য: পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিশুরা ধুতি ও শাড়ি পরে কৃষ্ণ – ও রাধা সেজে নদীর পাড়ে এই নৃত্য পরিবেশন করে।
- আদিবাসীদের লোকনৃত্য: আদিবাসিদের উৎসব ‘করম পরব’, – ‘বনা পরব’, ‘ফাগের উৎসব’-এ ছেলে ও মেয়েরা একসাথে দল বেঁধে – কোমরে কোমরে হাত দিয়ে তিন-তিন ছন্দে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। – তাদের প্রচলিত গানগুলি গাওয়া হয় সহযোগী যন্ত্র হিসেবে মাদল, ধামসা, বানাম, বাঁশী ব্যবহার করা হয়।
- শুদুমা নৃত্য: উত্তর বাংলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচলিত। মেয়েরা বৃষ্টির আশায় সমবেতভাবে এই নৃত্য পরিবেশন করে। শিল্পী নৈপুণ্যের থেকে আবেশ প্রাধান্য পায়।
- গম্ভীরা নৃত্য: গম্ভীরা বাংলার লোকনৃত্যের ভান্ডারে একটি রত্ন। চৈত্রমাস জুড়ে মালদহ জেলায় এই উৎসব চলে। গম্ভীরা অর্থ শিব। এই উৎসব গম্ভীরা নৃত্য সহযোগে যে গান গাওয়া হয় তা শিবেরই গান। গম্ভীরা গানে শিবকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপাত্মক গান গাওয়া হয় তাই এই নাচও বিদ্রুপাত্মক হয়। মূল গায়েনের মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধে হাতে পায়ে সাদা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যান্ডেজ করা থাকে। এই নৃত্য দেখলে হাস্যকর হলেও শিবের কাছে তাদের অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করেন। মূল গায়েনের সাথে যারা নৃত্য করে তারা সাধারণ বেশভূষায় শিবের চারপাশে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করেন।
- বাউল নৃত্য: বাউল গানের সঙ্গে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। গান গাইতে গাইতে একতারা বাজিয়ে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে নিচু হয়ে কোমর ঘুরিয়ে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাউলের আলখাল্লার উপর উত্তরী বেধে পায়ে ঘুঙুর দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন। গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই গান ও নাচ যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে।
- নামকীর্তনের নৃত্য: বৈষ্ণবরা শ্রীখোল বাজিয়ে দুবাহু তুলে নাচতে নাচতে দলবেধে ঘুরে বেড়ায় তা বাংলার নিজস্ব। এই নৃত্যে ভক্তির সঙ্গে ভাবের সমন্বয় ঘটে।
- ছৌ নৃত্য: পুরুলিয়ার মাহাতো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নৃত্য বহুল প্রচলিত। আমাদের এই ছৌ নৃত্য পৌরানিক আখ্যান যেমন-দুর্গা, কালির উপখ্যান এবং ইতিহাসের ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত। এই নৃত্য হাত পায়ের অঙ্গ সঞ্চালনের চাইতে দৈহিক অনুশীলনের দিকটাই প্রাধান্য পায়। 2019 সালে Heritage দ্বারা ছৌ নৃত্যকে Intangible Cultural Heritage লিস্টে অন্তভুক্ত করা হয়।
- নটুয়া নৃত্য: পুরুলিয়া অঞ্চলে জনপ্রিয় এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। ছৌ নাচের মতোই দৈহিক এর মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্য মুখোশ এর পরিবর্তে রঙ মাখার প্রচলন রয়েছে।
- গাজন নৃত্য: শিব উৎসবের মধ্যে ভক্তেরা নানা প্রকার সাজে গাজন গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে গ্রামাঞ্চলে।
বাংলার নাটক:
বাংলায় লোকনাট্য গ্রাম বাংলায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলন থাকলেও নাটকের প্রকৃত জাগরণ শুরু হয় বলা যায় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইংরেজ রঙ্গমুক্ত প্রতিষ্ঠা করে নাটক পরিবেশনে উদ্বদ্ধ হয়ে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রথম 1831 সালে হিন্দু, থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রথম পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয় 1872 সালে ‘ন্যাশানাল থিয়েটার’ নামে। এই সময়ের প্রধান নাট্যকার ছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ।
এই সকল পেশাদারি থিয়েটার ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাত ধরে বাংলার নাটকে নবজাগরণ শুরু হয়। এরপর নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এর উদ্ভব হয়। বিশ শতকের শুরুর পর বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করেন বিভিন্ন নাট্যকারগণ। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ জাতীয় চেতনার প্রয়াসে হয়ে উঠেছিলেন তৎপর।
1930 দশকে নাট্যকারগণ সমাজ সচেতনতা, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ের নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সময়ের নাট্যকার ছিলেন মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ।
1943 সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়ে উঠল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বারা বাংলার নাটক নতুনভাবে উজ্জীবিত হল। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখ শুরু করলেন গণনাট্য আন্দোলন, নাটকে স্থান পেলো রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা। এই ধারার বাইরে বিদেশী নাটকের ভাবধারায় নাটক রচনা করলেন বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ।
স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে উঠে এলো নানা গ্রুপ থিয়েটার। গণনাট্য সঙ্ঘের ভাবধার লেখা এই নাটকগুলির বেশীর ভাগ বামপন্থী আন্দোলন মুখি। তবে বেশ কিছু ব্যক্তি বাংলার সমাজ কেন্দ্রীক নাটক এই সময় করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মনোজ মিত্র।
মাইকেল মধুসুদন: মাইকেল মধুসুদন দত্তের নাট্য প্রতিভা ছিল কাব্য প্রতিভার মধ্যেই যুগান্তকারী। তিনি পাশচাত্য নাটকের অনুকরণে সার্থক নাটক লিখে বাংলার নাট্য-সাহিত্যের পথকে সুনির্দিষ্ট করে যান। 1859 সালে পুরাণ এর কাহিনী অনুসরণে শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। 1860 সালে প্রকাশিত কৃষ্ণকুমারী তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। তাঁর রচিত প্রহসন হল-‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’।
দীনবন্ধু মিত্রঃ দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল মধুসুদন এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও মাইকেলী যুগের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার রুপে আখ্যায়িত হয়েছেন। 1860 সালে প্রকাশিত ‘নীলদর্পন’ বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় গ্রন্থ। এই নাটক বহুসাহিত্যের বাস্তবতার পথ নির্দেশ করেছিল। ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের দ্বারা নীল চাষিদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রকাশিত অন্যান্য নাটক ও প্রহসনগুলি হল- নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগল বুড়ো ইত্যাদি।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে ছিলেন। বাংলা নাটককে সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত করেছিলেন। হিন্দুমেলা থেকে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয়দের স্বদেশ প্রীতি বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ভারতবর্ষের গৌরবকাহিনী বর্ণনা করেছেন- পুরুবিক্রম (1878), সরোজিনী (1875) অশ্রুমতি (1879) নাটক।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ: বাংলার নাট্যজগতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, তিনি ছিলেন রঙ্গমঞ্চের সংস্কারক এবং পরিচালক। তার পূর্বে বাংলার নাট্যজগৎ শৈশব স্তরে ছিল। পূববর্তী নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিভিন্ন প্রকার নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকে দেশীয় ও জাতীয় প্রভাব বেশী থাকলেও তিনি বিদেশীভাব ও আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। শেক্সপিয়ারের মতো তিনিও নাটকে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ মেনে চলেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব গৈরিশী ছন্দ ব্যবহার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হল- বিল্বমঙ্গল, পান্ডব-গৌরব, প্রফুল্ল, বলিদান ইত্যাদি।
উৎপল দত্ত: নাট্যাভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। চরিত্রের রুক্ষ ও রূঢ় রূপের যথাযথ বর্ণনায় তাঁর নাট্য বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ও তার নাটকে তার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। তার রচিত বিখ্যাত নাটক হল-ছায়ানট, অঙ্গার, ধূমকেতু, ফেরারী ফৌজ ইত্যাদি।
বাদল সরকার: নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বাদল সরকার। কৌতুকর্ণাকে দিয়ে তিনি পথচলা শুরু করেন। পরবর্তীকালে অ্যাবসার্ড নাটক রচনা করেও সাফল্য অর্জন করেন। তার রচিত নাটকগুলি হল বড়ো পিসীমা, -রাজশ্যাম যদু এবং ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি।
শম্ভুমিত্র: তিনি ছিলেন নাট্য প্রযোজক নাট্য সংগঠক এবং একই সাথে – সফল নাট্যকার। মাত্র 24 বৎসর বয়সে নাটকে অভিনয় শুরু করেন। 1941 – সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ‘উলুখাগড়া’ নাটক লেখেন। পরবর্তীতে আরও দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন যথা- ঘূর্ণি ও চাঁদ বণিকের পালা। সফল মঞ্চভাবনার পাশাপাশি তিনি তাঁর সমকালীন সমাজ মনস্কতার ভাবনা এই নাটকগুলিতে তুলে ধরেছেন।
তৃপ্তি মিত্র: 1943 সালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়। তিনি অভিনয়ের সঙ্গে নাট্য রচনাতেও তার দক্ষতার স্বাভব রেখে গেছেন। তার রচিত নাটকগুলি হল- বলি, ইঁদুর, সুতরাং, প্রহরশেষে, কে বাঁচে?, কে ও বিদ্রোহিনী।
বাংলা সাহিত্য:
বাংলা ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। – উত্তর-উত্তর-পূর্ব হিমালয় দ্বারা পরিবেশিত ও পশ্চিমে মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত – বৈচিত্র্যময় ভূমিভাগের মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম বাংলা ভাষা। মৌর্য – যুগের পর প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও বৈদিক মতবাদের প্রচার এই অঞ্চলে শুরু হয়। উত্তর ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও মাগধী প্রকৃত ভাষার প্রভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, অচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাল যুগে মাগধী – প্রাকৃত ও এই অঞ্চলে প্রচলিত অপভ্রংশ এর মিশ্রনে নতুন দেশীয় ভাষায় উদ্ভব ২ হল। বর্তমান বাংলা ভাষায় এটিই হল আদিরুপ। রচিত হল চর্যাপদ। চর্যাপদেররচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার সাহিত্যকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়।
প্রাচীনযুগ (950 খ্রীঃ -1350 খ্রীঃ):
পাল ও সেন রাজাদের সময় বাংলাভূমিতে অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য চর্চা হত। জনসাধারণ ও বৌদ্ধ ধর্ম গুরু ও শৈবনাথ পন্থী ধর্মগুরুরা এই ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করতেন। তাদের রচনা গুলিই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যুগের রচনা। খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা জন্মগ্রহন করে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা এই ভাষায় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা, সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সাধন প্রণালীর পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র এর বর্ণনা ‘চর্যাপদ’ এ বর্ণনা করে গেছেন। আনুমানিক 900 খ্রীঃ থেকে 1200 খ্রীঃ এর মধ্যে চর্যাপদগুলির রচনা বলে মনে করা হয়।
মধ্যযুগ (খ্রীঃ 1350-1800 খ্রীঃ):
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, মুকুন্দ, দৌলতকাজী, আলাওল, রামপ্রসাদের মতো প্রখ্যাত কবিগন তাঁদের কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।
বাংলার স্থায়ী সুলতানি শাসনের ফলে জন্মাসনে সুস্থিতি বিরাজ করলে এর প্রভাব সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে লাগল। উচ্চ ও নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক মিলনের ফলে জাতি হিসাবে বাঙালির স্বরূপ সুস্পষ্ট হল। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাগুলি চলতে লাগল-
অনুবাদ: অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি ভাষায় লেখা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষত রামায়ন-মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হল। রামায়নের অনুবাদে কৃত্তিবাস ওঝা মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ ধারার প্রথম কবি। তিনি বাল্মীকি রামায়নের অনেক প্রচ্ছদ পরিত্যাগ করেছেন ও রামায়নের কাহিনীকে বাংলার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু। পঞ্চদশ শতকে তিনি সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বদ্ধ অবলম্বন করে ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচনা করেন। দুটিমাত্র স্কন্ধ নির্বাচনের পেছনে কবির শিল্পবোধ সক্রিয় ছিল বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণ আর্বিভাবের কারন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার কীর্তিকলাপই তিনি বর্ণনা করেছেন।
গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এর সভাকবি ছিলেন কবিন্দ্র পরমেশ্বর। তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত মহাভারত পরাগলি মহাভারত নামে পরিচিত।
মঙ্গলকাব্য: পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চার শত বৎসর ধরে বহু কবি এই কাব্য শাখায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছেন। ফলে মঙ্গলকাব্যগুলি দেবদেবীদের লৌকিক পাঁচালী কাব্য। মনসাপূজার সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও বিস্তার। মনসাপূজা উপলক্ষেই মনসামঙ্গল ‘ভাষান’ বা ‘রয়ানি’ হিসাবে পাওয়া যায়। 1494 সালে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে তাঁকে মনে করা হয়। বিপ্রদাস পিপলাই তার রচিত মনসামঙ্গল কাব্যকে ‘মনসা বিজয়’ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন।
বৈষ্ণব সাহিত্য:
তুর্কি বিজয়ের আগে স্বদেশে পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মী, সরস্বতী গুরুড় সহ পূজ্য হতো। পরবর্তীকালে চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্ম নতুন রূপ নিয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্যের দুটি উপশাখা- (ক) কৃষ্ণলীলা কাব্য (খ) পদাবলী কাব্য। দুটি স্বতন্ত্র ধারা হলেও এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ নৈকট্য ছিল। চৈতন্যপূর্ব বাংলায় পুরানানুগকৃষ্ণকাহিনী প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কৃষ্ণলীলা, কাব্যের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য যার রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। এই কাব্যের কাহিনী এগারো খন্ডে বিভক্ত, তবে শেষটুকু পাওয়া যায়নি। এই কাব্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক বৈষ্ণব কবিতা একটি সমৃদ্ধ ধারা সৃষ্টি করেছিল এবং চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে এই ধারায় প্রাণ চাঞ্চল্য আসে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদগুলি বাংলাদেশে ছিল আশ্চর্য জনপ্রিয়। তিনি বৈষ্ণবপদাবলি সমাজে মহাজনরূপে পূজা পেয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় জনপ্রিয় ছিলেন চন্ডীদাস। তাঁর কবি প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য গীতিপ্রাণতা।
ইসলামী সাহিত্য:
পঞ্চদশ শতক থেকে মুসলিম লেখকগন বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। শাহ মহম্মদ সগির বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। তার লেখা ইউসুফ জেলেখা একটি ইসলামী কাব্য। ষোড়শ শতকে সৈয়দ সুলাতন ‘নবীবংশ’ রচনা করেন। নবীবংশের প্রথম খন্ডে বিভিন্ন নবীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় খন্ডে হজরত মহম্মদের জীবনী বর্ণনা করেছেন। সপ্তদশ শতকে কবি শেখ চন্দে-নবীবংশে এর আদলে ‘রসুলনামা’ বা ‘রসুল বিজয়’ লিখেছেন। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে আবদুল নবী ‘আমীর হামজা বিজয়’ রচনা করেন। মহম্মদ খান-‘মঞ্জুল হোসেন’ নামে কারাবালা যুদ্ধ নিয়ে একটি বিপুল আকৃতির কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগে বাহরাম খান লায়লা মজনু কাব্য রচনা করেন। তিনি করুন রসের কবি ছিলেন। আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে দৌলত কাজি, আলাওল প্রমুখ বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্য রচনা করেন।
সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতি ও জীর্ণ হয়ে পড়লো। মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি যোগ্য শাসক হলেও সাহিত্যচর্চায় বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। আলিবর্দির সময়কালে বসিহানায় পদ্মার প্রাচীনতার পর্যন্ত বিধ্বস্থ হয়েছে। 1757 এরপর বাংলার শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে গেলো এবং কলকাতা হল ভারতের রাজধানী ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র।
আধুনিকযুগ (1800 খ্রীঃ বর্তমান):
কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালী সমাজ-এর ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটার মধ্য দিয়ে ইউরোপের সাংস্কৃতিক নিকটবর্তী হল। এর ফলে দেশীয় চিন্তায়, কার্যে ও সৃষ্টিতে যে নতুনত্ব দেখা দিলো তাকেই নবজাগরণ আখ্যা দেওয়া হয়।
1800 খ্রী: ৪ঠা মে ব্রিটিশদের দ্বারা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। বিদেশ থেকে আগত ইংরেজ কর্মচারিদের দেশীয় ভাষায় পারদর্শী করে তোলার জন্যই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যের প্রভুত উপকার সাধন করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যে সকল আধ্যাপকগণ বাংলা গদ্যের পরিকাঠামো নির্মানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারা হলেন উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়, চন্ডীচরণ মুন্সি প্রমুখ।
উইলিয়াম কেরী এই কলেজে 1801-1838 সাল পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান রূপে বর্তমান ছিলেন। তাঁর হাতে সৃষ্ট অনবদ্য বাঙলা গ্রন্থ হল কথোপকথন, ইতিহাসনামা। আধ্যাপক রামরাম বসু বাংলা গদ্যকে উপহার দিয়েছিলেন ‘রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ ও ‘লিপিমালা’। আধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল- বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, প্রবোধ চন্দ্রিকা ও বেদান্ত চন্দ্রিকা। 1854 খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিলুপ্তি ঘোষনা করা হয়। এই কলেজ পরোক্ষ ভাবে বাংলা গদ্যের প্রভুত উপকার করেছিল।
বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারায় ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় প্রায় 30 টি বাংলা গদ্য রচনা করেন। তাঁর বিরাট রচনার সম্ভারকে অনুবাদমূলক ও মৌলিক রচনা ভাগে ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য তিনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ গ্রন্থ গুলি হল-বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, উপনিষদ ইত্যাদি। সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন- ভট্টাচার্যের সহিত ও বিচার, গোস্বামীদের সহিত রচিত ইত্যাদি।
বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সার্থক রূপকার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজ সংস্কার ও নারী শিক্ষায় প্রচলন এর উদ্দেশ্যে তিনি আজীবন প্রচেষ্টা করে গেছেন। তাঁর রচিত অনুবাদমূলক রচনাগুলি হল ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘শকুন্তলা’, ‘সীতার বনবাস’, ‘ভ্রান্তিবিলাস’ ইত্যাদি। তিনি ছিলেন বাংলা সাধুগদ্যের শ্রষ্ঠা। বিরূম চিহ্নের ব্যবহার দেখিয়ে বাংলা গদ্যকে সহজ সরল ও বোধগম্য পূর্ণ করেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে ‘কবি সার্বভৌম’ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার নাট্য সাহিত্যে নতুন ধারা যথা কাব্যনাট্য, সংকেত-রূপকন্যাট্য-এর সূচনা করেছেন তিনি। উপন্যাস সাহিত্যে ক্ষুদ্র উপন্যাস ধারার সূচনা করেন। বাংলা ছোট গল্প প্রকৃত রুপসিদ্ধি লাভ করল তাঁর হাত ধরেই। কাব্য ও কবিতার ক্ষেত্রেও নানা প্রকার বিচিত্র নবীনতা নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম কাব্য ‘কবিকাহিনী’ 1878 সালে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত শেষ কাব্য ‘জন্মদিনে’। 60 বৎসরের ও বেশী সময় তিনি অজস্র কাব্য-কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। 1878 সাল থেকে 1882 সালের মধ্য প্রাথমিক স্তরে রচিত কাব্যগুলির অন্যতম হল- কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, ভানু সিংহের পদাবলী এরপর প্রকাশিত কবিতা ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান এ কবির পরিণত লেখার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান সুর কাল্পনিক সৌন্দর্য-বিরত্বের বেদনা প্রকাশ। তার জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ক সুগভীর ভাবনা কবিতায় রুপ পেয়েছে। ‘সোনার তরী’ থেকে কণিকা পর্যন্ত কবি সৌন্দর্য বিহ্বলতা ও মর্ত্য প্রেমের গান করেছেন। খেয়া ও গীতালি পর্যন্ত অমর্ত্যলোকের সুর শোনা যায়।
রবীন্দ্রনাথ ছোট-বড় বারোখানা উপন্যাস লিখেছেন। বঙ্কিম প্রবর্তিত ধারায় তিনি উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হলেও সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসে তার সাফল্য অনেক বেশী। বউ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি ঐতিহাসিক রোমান্স রূপে বিবেচিত হয়। সামাজিক উপন্যাস এর মধ্যে অন্যতম চোখের বালি, নৌকাডুবি এবং গোরা।
বাংলার ছোট গল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার ছোট গল্পে পরিবার জীবনের চিত্র সমাজ সমস্যার কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত ছোট গল্পের মধ্যে অন্যতম হল বাঙ্কাল, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, বিচারক, মণিহারা।
প্রবন্ধ-সাহিত্যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, শিক্ষা, স্বদেশ, কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্ববর্তী উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি নিজের মানস প্রবণতা অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টিও করেছেন। তার রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের নৈমিত্তিক ঘটনা, সুখ ও দুঃখ। তিনি পারিবারিক জীবনের রূপকার। তার বড় গল্প যেমন রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, মেজদিদি ইত্যাদি পরিবার জীবনের কাহিনী ওসমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার পল্লীগ্রামের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলে। পল্লীগ্রামের মানুষের বিভিন্ন স্বভাব-পরশ্রী কাতরতা, স্বার্থপরতা, সরল হৃদয়তা, উদারচিত্ত এর সুন্দর বর্ণনা করেছেন চরিত্রের মাধ্যমে।
কাজী নজরুল ইসলাম অধিকাংশ কাব্য রচনা করেছেন 1922 থেকে 1930 এর মধ্যে। এই কাব্যগুলি হল অগ্নিবীনা, ভাঙারগান, বিষের বাঁশী, সর্বহারা ইত্যাদি। 1930 থেকে তিনি গীত রচনায় মন দেন। নজরুল ছিলেন সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষন মুক্ত ভারতের স্বপ্ন, সর্বস্তরের শ্রমজীবি মানুষ এবং বঞ্চিত জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। নজরুল বিদ্রোহের কবি। তাঁর কবিতায় আরবি-ফরাসি শব্দের ও বাগ্ ধারায় স্বাভাবিক ও সুনিপুণ ব্যবহার ও হিন্দু পুরাণাদির জগৎ স্থান পেয়েছে। ফলে হিন্দু পাঠকেরা যেমন সাবলীলভাবে বাংলা কবিতার ইসলাম পরিমন্ডলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তেমনি মুসলমান পাঠকেরাও বাংলা কবিতাকে আপনাদের বস্তু বলে ভাবতে পেরেছে।
বাংলার উপভাষা:
বাংলা ভূমিতে (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) যে জনগোষ্ঠী বাস করে তারা প্রধানত বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভাব বিনিময় করে ও লেখালেখি, সাহিত্যচর্চাও করে। এই জনগোষ্ঠীকে বাঙালী ভাষা সম্পদের হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষায় প্রভেদ দেখা যায়। পূর্ব মেদিনীপুর ও কোচবিহারের মানুষের মৌখিক ভাষার বিস্তর পার্থক্য। এদের সাহিত্যের ভাষার প্রভেদ না থাকলেও কথ্য বা মৌখিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে, এরই নাম উপভাষা (Dialect)। অঞ্চলভেদে বাংলা উপভাষাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
- রাঢ়ী: গঙ্গা ও ভাগীরথী সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা ‘রাঢ়ী’ নামে পরিচিত। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই উপভাষার প্রচলন।
- বরেন্দ্রী: পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র সন্নিহিত উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী নামে পরিচিত। মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চল বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত।
- কামরুপী: ব্রহ্মপুত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন উত্তর-পূর্বের উপভাষা কামরুপী নামে পরিচিত। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে এই উপভাষায় মানুষজন কথা বলেন।
- ঝাড়খন্ডী: ‘ঝাড়খন্ড’ অঞ্চলের উপভাষা ‘ঝাড়খন্ডী’। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভূম, মানভূম, বলিভূম অঞ্চলের কথ্যভাষা ঝাড়খন্ডী।
- বঙ্গালী: পদ্মা ও ভাগীরথীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা বাঙালী। যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি, বরিশালে এই ভাষায় কথা বলে।
বাংলার মেলা ও উৎসব:
মেলা ও উৎসব হল মানব সমাজের দর্পন। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে এই মেলাগুলি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। বাংলার এই মেলা ও উৎসবগুলির দুটি দিক রয়েছে। এক গ্রামীণ বাংলার মেলা ও উৎসব-যেখানে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-রুচি, শিল্প-সাহিত্যের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন গাজন, রথের মেলা, চড়ক মেলা ইত্যাদি। গ্রাম ও শহরে মেলা ও উৎসবের ধারাটি সময়ের বিবর্তনে নানান বিষয়ের অংশ হয়ে উঠেছে যেমন দুর্গোৎসব।
কেন্দুলিমেলা: বীরভূম জেলায় কেন্দুলি গ্রামে রাধাগোবিন্দ মন্দিরকে কেন্দ্র করে অজয়ের তীরে এই মেলা হয়। কবি জয়দেবের জন্মভূমিও স্মৃতিবিজড়িত এই মেলা। কথিত আছে কবি জয়দেব মা গঙ্গার দর্শন পেয়েছিলেন এই অজয়ের ঘাটে এক পৌষ-সংক্রান্তির দিন। মা গঙ্গার দর্শন পেয়ে আনন্দিত কবি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করেন। প্রত্যেক বৎসর ওই দিনেই কেন্দুলিতে বৈষ্ণব সমাগম ও মেলার প্রচলন হয়। বর্তমানে কেন্দুলির মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বাউলদের সমাবেশ। স্থানীয় লোকশিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত কাঠের পুতুল, লাভার পাখি পুতুল, গহনা মেলায় বিক্রয় হয়।
গাজনের মেলা: গর্জন শব্দ থেকে ‘গাজন’ হয়েছে। গাজন উৎসবের মধ্যে মহাদেব-শিব কে আহ্বান করার ধ্বনি গর্জনের মতোই শোনায়। চৈত্র মাসের শেষদিকে রুদ্রদেবের গাজন উৎসব বাংলার বিভিন্ন স্থানে হয়। গাজনের সময় ব্রত পালন করে সন্ন্যাসী হতে হয়। প্রথমদিন সন্ধ্যাবেলায় কাঁটা ভাঙা দিয়ে পূজা অর্চনা শুরু হয়। এরপর সিদ্ধিভাঙা, চোরাজাগরন, মড়া-খেলা নৃত্য বিভিন্ন পালিত হয়। চড়ক উৎসব অর্থ্যাৎ পিঠে লোহার বড়শি লাগিয়ে গাছ থেকে ঝুলে প্রদক্ষিন করা এই গাজনের মেলার অংশ।
বসন্ত উৎসব: প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্নিমায় বাংলার দোল উৎসব বা বসন্ত উৎসব পালিত হয়। বাংলায় প্রতিটি অঞ্চলে পালিত হলেও বসন্ত উৎসব হিসেবে আন্তজার্তিক খ্যাতি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা পালিত শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব। শান্তিনিকেতনে দেশ-বিদেশের মানুষ এই দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যে বসন্ত উৎসব মুখরিত হয়।
রাসমেলা: 1812 সালে কোচ রাজারা ভগবান কৃষ্ণের আরেক রূপ মদন মোহনের সম্মানে এই উৎসব শুরু করেন। প্রতিবৎসর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেরাসপূর্নিমার দিন। এই মেলার শুরু হয় ও এক মাস ব্যাপী মেলা চলে। এই মেলাটি আর্ন্তজাতিক পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। মেলা শুরু হওয়ার সময় থেকেই নেপাল ভুটান থেকে মানুষ এই মেলায় যোগদান করত। এছাড়াও শান্তিপুরের রাসমেলা বিখ্যাত।
গঙ্গাসাগর মেলা: কুম্ভ মেলার পর সবচেয়ে বেশী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয় গঙ্গাসাগর মেলায়। প্রত্যেক বৎসর মকর সংক্রান্তির সময় দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরদ্বীপে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কপিল মুনি গঙ্গা ও সাগরের মিলন স্থলে তপস্যা করেন। সেই কপিল মুনির মন্দির কেন্দ্র করেই সঙ্গমস্থলে পূর্ণস্নান ও মেলার আয়োজন হয়। এই মেলা আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ সঙ্গম স্নান এর জন্য গঙ্গাসাগর মেলায় আসেন। রথের
রথের মেলা: বাংলার বিভিন্নস্থানে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে একসপ্তাহ ব্যাপি মেলার আয়োজন হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রা এর রথে চেপে মাসির বাড়ি যাত্রা ও একসপ্তাহ পর উল্টোরথ বা নিজের বাড়ি প্রত্যাবর্তন হয়। পশ্চিমবঙ্গের রথযাত্রার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা। শেওড়াফুলির রাজা মাহেশে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থদান করেন। বর্তমানেও মেলাটিতে অগনীত ভক্তের জনসমাগম হয়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নির্মিত দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা নজর কেড়েছে। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা বিখ্যাত। পুরীর পর সবচেয়ে বেশী দূরত্ব এই রথ অতিক্রম করে গুপ্তিপাড়ার রথের মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্টোরথের আগের দিনের মাসির বাড়ির ভান্ডার লুট।
উপসংহার:
বাংলা শিল্পকর্ম, কলা ও সংস্কৃতি বাঙালির জীবনচেতনা, ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার এক সমৃদ্ধ প্রতিফলন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলার শিল্পধারা নানা পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছে। গ্রামীণ লোকশিল্প যেমন নকসি কাঁথা, পটচিত্র কিংবা ডোকরা শিল্প সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস ও আনন্দ-বেদনার কাহিনি বহন করে। একইভাবে শাস্ত্রীয় ও আধুনিক শিল্পচর্চায় বাংলার অবদানও অনস্বীকার্য।
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি যেমন লোকজ ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর রবীন্দ্রসংগীত ও কাজী নজরুল ইসলাম-এর নজরুলগীতি বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে মর্যাদা এনে দিয়েছে। চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বেঙ্গল স্কুল জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। নাট্যচর্চা, যাত্রা, ছৌ নৃত্য প্রভৃতি ধারাও বাংলার সাংস্কৃতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে।
বাংলার উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশেষত দুর্গাপূজা, কেবল ধর্মীয় আচার নয়—এটি শিল্প, স্থাপত্য, সংগীত ও সামাজিক মিলনের এক বৃহৎ ক্ষেত্র। প্রতিমা নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও থিমভিত্তিক মণ্ডপ বাংলার সৃজনশীল শক্তির পরিচয় বহন করে। সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসভায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, যার অন্যতম প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার।
আধুনিক যুগে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এলেও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য অটুট রয়েছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে আজকের বাংলা শিল্প আরও বহুমাত্রিক হয়েছে। চলচ্চিত্র, আধুনিক সংগীত, চিত্রপ্রদর্শনী ও ডিজিটাল শিল্পচর্চা নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীলতার পথে উদ্বুদ্ধ করছে।
সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলা শিল্পকর্ম, কলা ও সংস্কৃতি কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়—এটি একটি চলমান সৃজনপ্রক্রিয়া। বাঙালির চিন্তা, আবেগ, মানবতাবাদ ও সৌন্দর্যবোধের ধারক ও বাহক এই সংস্কৃতি ভবিষ্যতেও তার স্বকীয়তা বজায় রেখে বিশ্বসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে। তাই এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসার করা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।
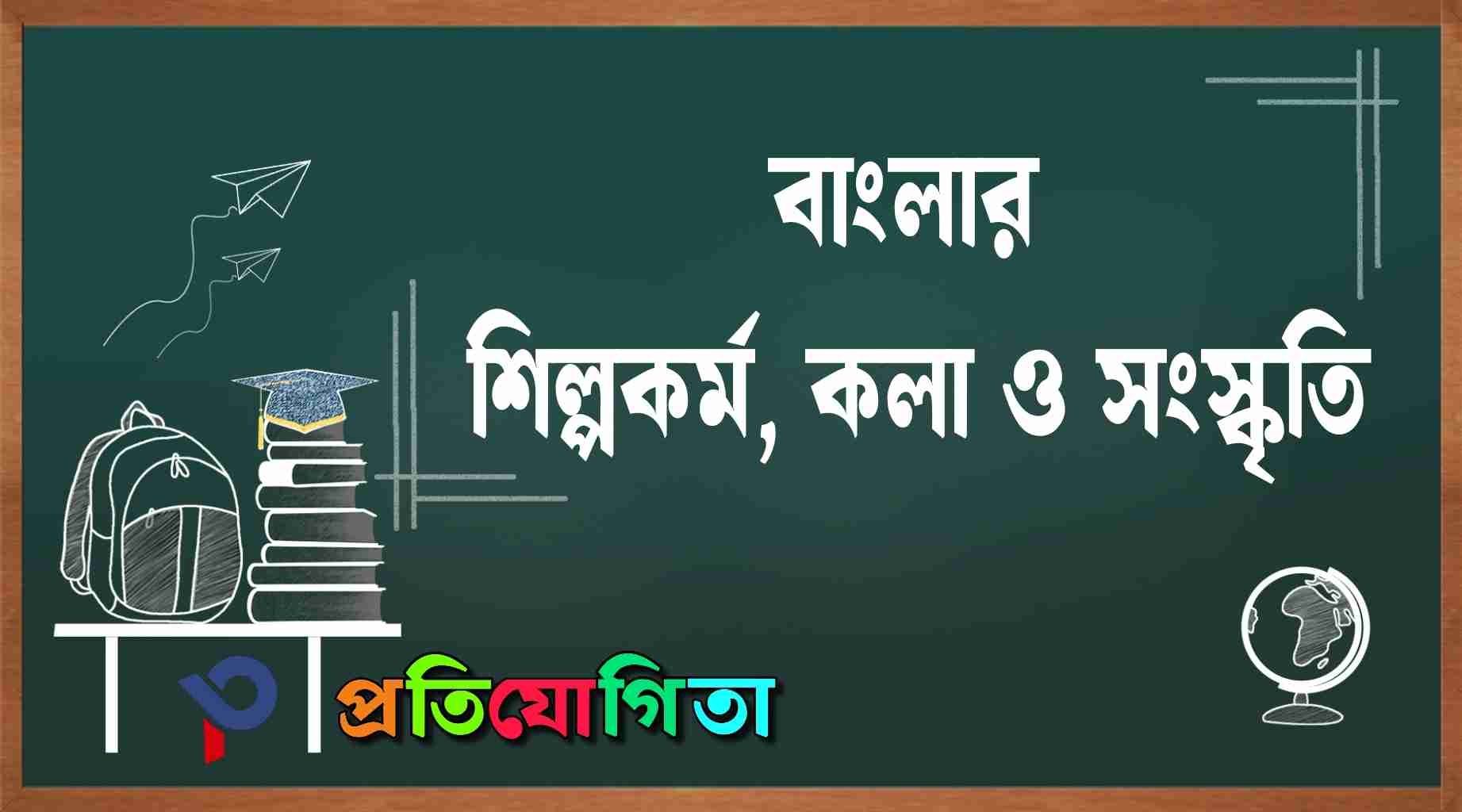
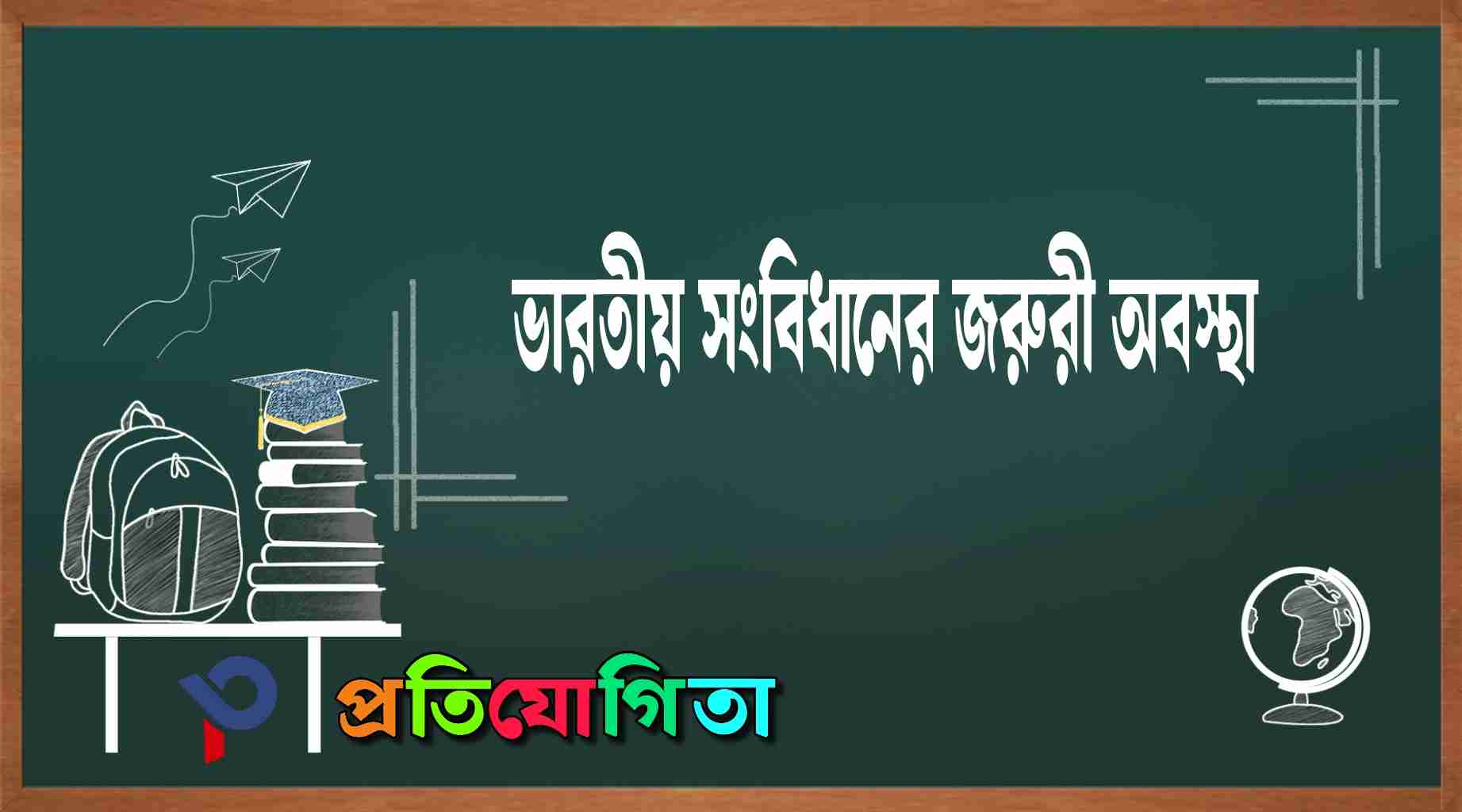
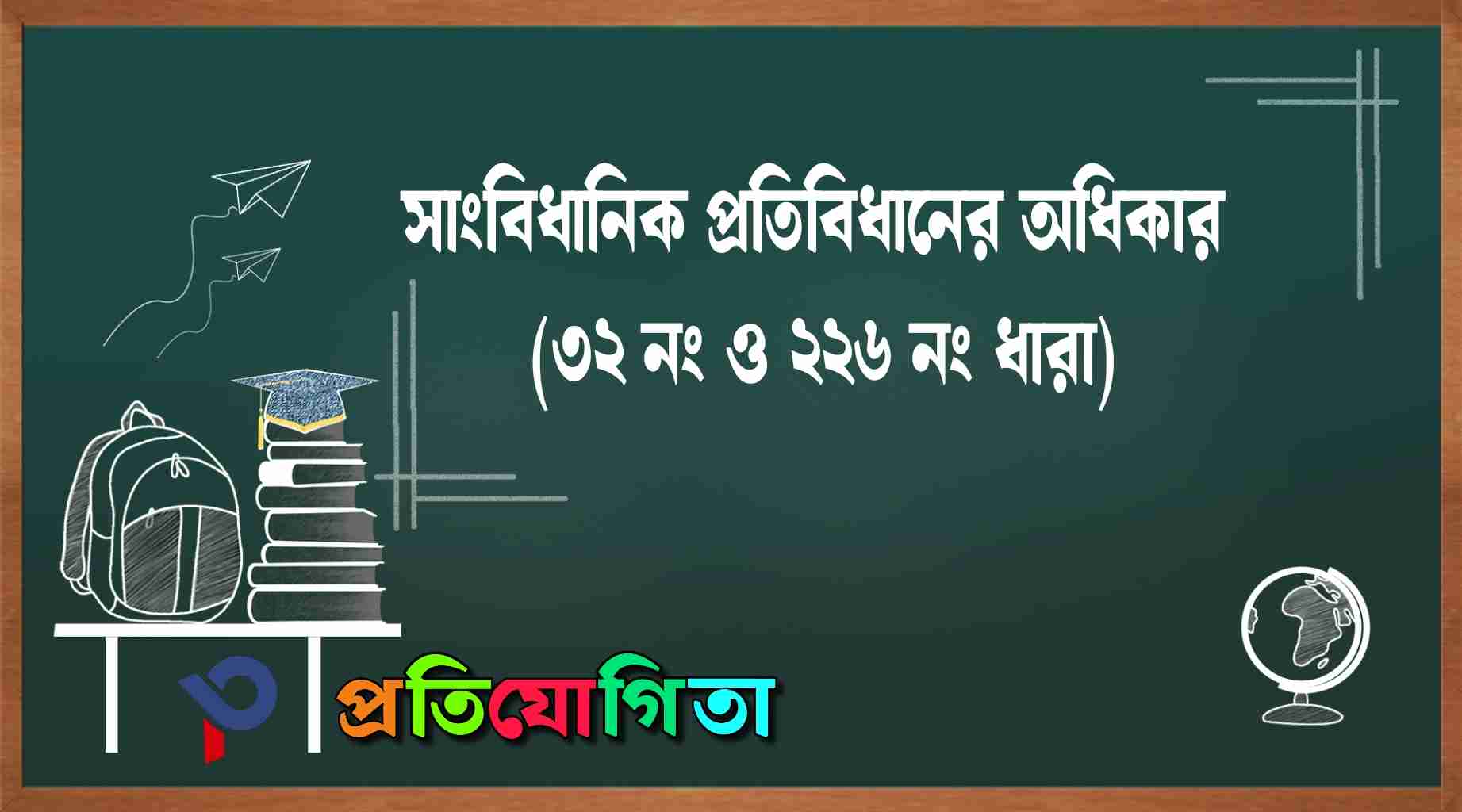
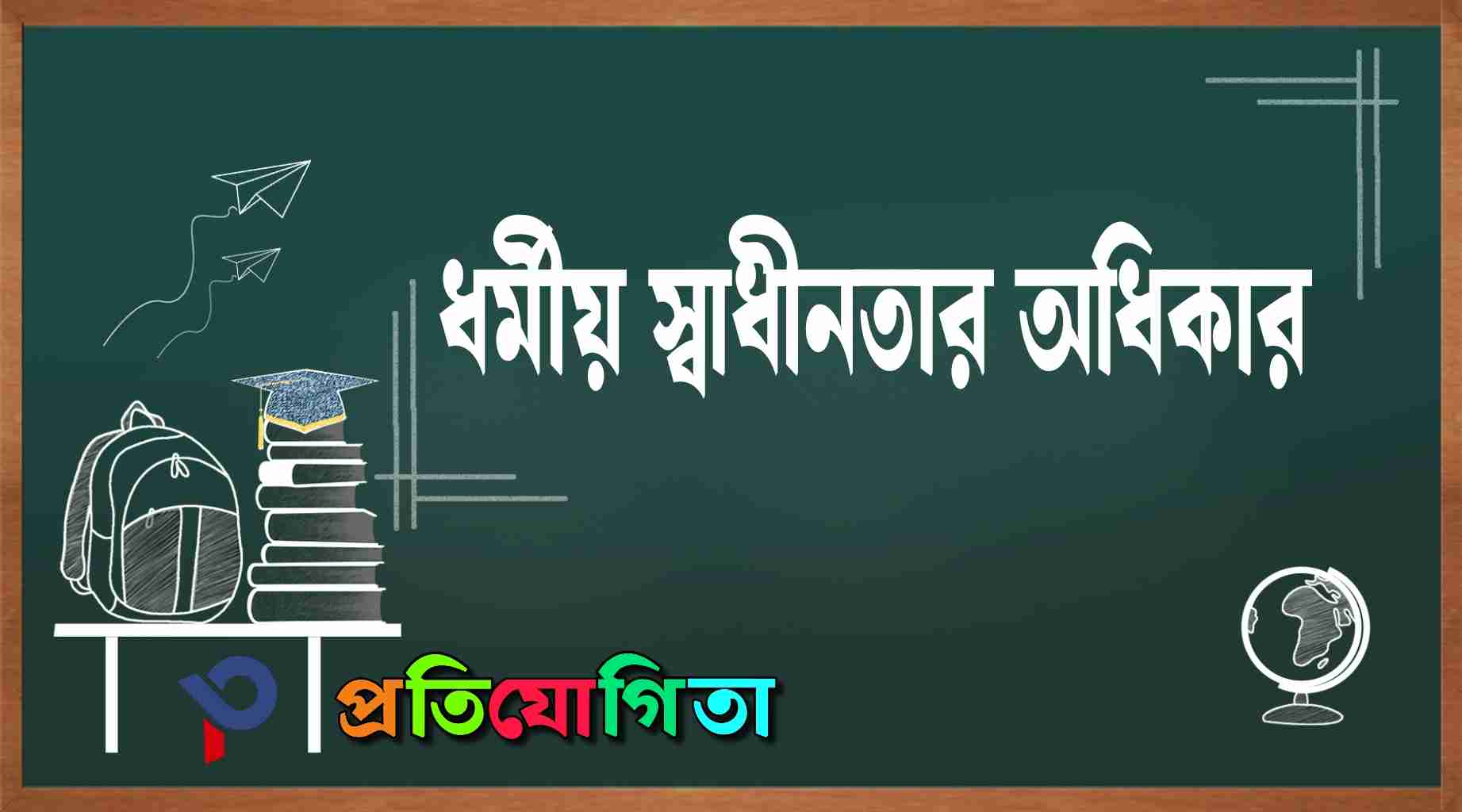










Post Comment